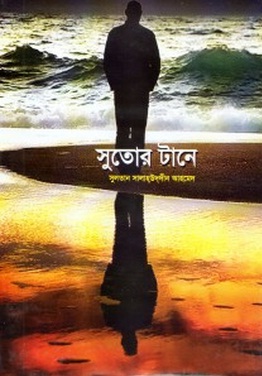|
সুতোর টানে-৫
সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ
দ্বিতীয় জীবন
মানুষের সবচেয়ে প্রিয় জীবনও যে কতোটা তুচ্ছ হয়ে ওঠতে পারে তা নিজেই
উপলব্ধি করলাম ১৯৭১ সালে। দেশের প্রতি ভালোবাসায় সাধারণ মানুষ
কীভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন তা হাজার পৃষ্ঠার বর্ণনাতেও বোঝানো যাবে
না। আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত যে সময়টিতে আমরা জাতিগতভাবে তৈরি
করেছি সেই সময়টিকে আমি কাছে থেকে দেখেছি। আমার পরম সৌভাগ্য সেই
সময়টির পেছনে আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।
১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন আমি ঢাকা কলেজে সেকেন্ড
ইয়ারে পড়তাম। পড়াশোনায় বেশ ব্যস্ত ছিলাম। আমরা তখন নিউ কলোনিতে থাকি।
কী করবো, একটা কিছু করে কীভাবে দেশের ভালো করবো তা নিয়ে সব সময়
চিন্তা করতাম। আমার বড় ভাই তখন ইন্ডিয়াতে চলে গেছেন মুক্তিযুদ্ধে
যোগ দিতে। আমরা দুই ভাই। চিন্তা করলাম, আমিও যদি চলে যাই তাহলে মা
বাবাকে কে দেখবে। তাই মা বাবার দিকে তাকিয়ে আমি থেকে গেলাম।
এই অবস্থায় থেকে কী করা যায় এমন চিন্তা ভাবনা সব সময় মনের ভেতর ছিল।
সে সময় মুক্তিযুদ্ধের নয় নাম্বার সেক্টরের গ্রুপ কমান্ডার মনোয়ার
আলীর সঙ্গে পরিচয় হয়। শুরুতে আমরা নয় নাম্বার সেক্টরে মেজর জলিলের
অধীনে ছিলাম। পরে আমাদের সার্টিফিকেট দেয়া হয় দুই নাম্বার সেক্টর
থেকে। জেনারেল ওসমানীর আত্মীয় ছিলেন মনোয়ার ভাই। রামপুরার দিকে একটা
জায়গায় তার সঙ্গে আমরা মিলিত হতাম। আমার ইচ্ছে ছিল মনোয়ার ভাই যেন
আমাকে একটা কাজ দেন।
এসময় আমরা আলাপ করলাম মুক্তিযুদ্ধ ঠিকভাবে চালানোর জন্য প্রচার
দরকার। এজন্য একটি ছাপার প্রেস প্রয়োজন। ডাবল ডিমাই প্রেস সব
জায়গায় পাওয়া যেত। সেই মেশিন আমরা কিভাবে দখল নিতে পারি সে আলোচনা
করি। তাহলে আমাদের লিফলেটগুলো ছেপে তা অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের
হাতে দিতে পারবো। আমি অবশ্য তখন পর্যন্ত ডাবল ডিমাই মেশিন দেখিনি।
তাই সবাইকে বললাম আমাকে আগে মেশিনটি দেখাতে। তখনো সকলের চিন্তা ছিল
কিভাবে মেশিন চুরি করা যায়। কিন্তু আমি আগে তা দেখতে চাচ্ছিলাম।
তারপর আমি মেশিনটা দেখলাম। মেশিনটা দেখে বাসায় এসে আমি চিন্তা
করলাম কিভাবে ছাপার মেশিনের বিকল্প বানানো যেতে পারে। যেটা করলে আমি
অনেক ছাপাতে পারব কিন্তু কেউই দেখে কিছু বুঝতে পারবে না। আমি তখন
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলাম। এখন হয়তো মনে হবে এটা
আমার মাথা থেকে বের হওয়া একটা বিস্ময়কর ঘটনা ছিল। এটা হয়তো আল্লাহর
রহমত। আমি প্রেস সম্পর্কে তখন কিছুই জানি না। শুধু জানি কালি দিয়ে
চাপ দিলে ছাপানো যায়।
আমি একদিন নিউ মার্কেটে গিয়েছি। গিয়ে দেখি যে একটা দোকান থেকে কিছু
কাগজ ফেলে দেয়া হচ্ছে। আমি দেখলাম যে অনেকগুলো কাগজ, কিন্তু সাধারণ
কোনো কাগজ নয়। তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা জানালো এটা হচ্ছে
স্ট্যানসেল। তখন আমি প্রথমবারের মতো জানতে পারলাম ছাপানোতে
স্ট্যানসেল বলে কিছু একটা আছে। স্ট্যানসেল হলো যেটা গেসটেটনার
মেশিনে লাগানো হয়। লাগিয়ে কালি দিয়ে ছাপানো হয়। তখন আমি গেসটেটনার
স্ট্যানসেল ডুপ্লিকেটর মেশিন কি তাই দেখেনি।
দোকানের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব ফেলে দিচ্ছেন কেন?
তিনি আমাকে জানালেন, এগুলো অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েছে, ছাপার কোনো কাজে
লাগে না। ডেট এক্সপায়েরড। তাই ফেলে দিচ্ছে।
আমি এগুলো নিয়ে যেতে পারি কি না অনুমতি চাইলে তারা সম্মতি জানালেন।
কাগজগুলো বাসায় নিয়ে আসলাম। শুরু হলো আমার গবেষণা।
ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার প্রথম রিসার্চ। এভাবে একদিন এ কালি ও কালি
ব্যবহার করে, ড্রাম কেটে তৈরি করলাম অদ্ভুত ধরনের একটা বিরাট মেশিন।
যেটা নাকি ইচ্ছা করলে খোলা যায় আবার এক সঙ্গে লাগিয়ে ছাপা যায়।
ওখানে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করি । পিভিসি পাইপ ছিল কলোনির
সামনে। সেগুলো রাতে কাটলাম। চট, স্পঞ্জ এবং ফ্যানেল ব্যবহার
করেছিলাম। এই তিনটার কম্বিনেশনে কালিটা গেলে পরে কালিটা ওখানে আটকে
থাকে এবং চাপ দিলে কালিটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে যখন
কলম দিয়ে দাগ কাটলাম এবং দাগের ফাঁক দিয়ে কালি বেরিয়ে আসল এবং
কাগজের মধ্যে ছাপাটা দেখলাম। খুবই উত্তেজনা এবং আবিষ্কারের একটা
সত্যিকারের অনুভূতি তৈরি হয়েছিল। তাহলে আমি পারবো। একটা কাগজে যদি
আমি লিখি তাহলে সেটা অনেকগুলো কপি করতে পারছি।
এরপর কিছু কাগজ আমি লিখে ছাপালাম এবং মনোয়ার ভাইকে দিলাম।
আমি তাকে বললাম, আপনাদের মেশিন চুরি করার দরকার নেই। সেটা করতে গেলে
অনেক মানুষ দরকার। তার চাইতে ভালো আপনারা যা ছাপাতে চান আমি ছাপিয়ে
দেবো।
মুক্তিযুদ্ধে যে কাগজগুলো ঢাকায় বা বাইরে দেয়া হতো সেগুলো আমি
বাড়িতে বসে ছাপতে থাকি।
মনোয়ার ভাই একদিন আমাকে বললেন, তুমি তো অনেক কিছু করছ।
আমি বললাম, না আমি কিছুই করিনি।
মনোয়ার ভাই বললেন, না তুমি অনেক কিছু করেছ। তোমার মেশিনটা আমরা
দেখতে চাই। আমি বললাম, আপনি যা চান আমি সব ছাপিয়ে দিব কিন্তু
মেশিনটা আমি কাউকে দেখাব না।
কারণ হচ্ছে আমার কাছে ভয় লাগলো, আমার এ মেশিন দেখতে তারা বাসায় আসবে।
আর বাসায় আসলেই মা বাবা সব জেনে যাবেন। আর আশেপাশের লোকজনও তাদের
দেখে ফেলবে।
প্রতিদিন আনুমানিক ৮০ কপি আমি করতাম। আমার হাত ব্যথা হয়ে যেত। বিলি
করার সময় আমি কিন্তু ৭০-৮০ কপি একসঙ্গে বিলি করতাম না। কপিগুলো নিয়ে
নিউ কলোনিতে একটি লন্ড্রিতে রাখতাম। দোকানের লোকটার কাছে আমি অল্প
অল্প করে জিনিসগুলো রাখতাম। তিনি জানতেন না যে প্যাকেটের ভেতরে কী
আছে। ওখান থেকে আমি আবার অন্য এক ছেলের কাছে জিনিসগুলো রাখতাম। সে
আবার আর একজনকে দিতো। এভাবে এক একজনের হাতের মাধ্যমে যেত। ফলে কোথা
থেকে জিনিসগুলো যাচ্ছে তা বোঝা যেত না। মনোয়ার ভাইয়ের লোক ওদিকে
ছিল। তারা আবার বিলি করতো। এভাবে আমাদের টার্গেট ছিল পুরো ঢাকা শহর
ছড়িয়ে দেয়া।
যখন আমরা কাগজ বিলি করতাম তখন আমার কাছে এটা যুদ্ধ বলে মনে হতো না।
মনে হতো আমি অ্যাকশন রিলেটেড কিছু কাজ করছি।
আমার ড্রাইসেল এবং গ্রেনেডের ট্রেনিং আগেই ছিল। মুক্তিযুদ্ধ যখন
প্রথম শুরু হয় সেই সময় মনোয়ার ভাইয়ের কাছ থেকে এগুলো শিখি আমি।
আমাকে ইন্ডিয়া যেতে হয়নি। আমি মনোয়ার ভাইকে খুব অনুরোধ করতাম আমাকে
একটা অপারেশন দেন। কাজ দেন। তিনি রাজি হন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি
আমাকে ধানমন্ডি সাব পাওয়ার স্টেশনে গ্রেনেড হামলা করতে দেন।
আমি সফলভাবে গ্রেনেড হামলা করি। হামলা শেষে দৌড়ে আসার সময় দেখি
আমাদের নিউ কলোনির নিচতলার চৌধুরী সাহেব পথে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি
শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছেন। পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে তার যোগাযোগ
ছিল। যা আমরা আগেই জানতাম। তিনি আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে
রইলেন।
আমার মনে হলো বাসা থেকে দ্রুত সরে যেতে হবে। বাসায় ঢুকেই কিছু
কাপড়-চোপড় নিয়ে মগবাজারে চলে যাই কবি আহসান হাবীবের বাসায়। সে সময়
তিনি মগবাজারে চলে গিয়েছেন। আমাকে তিনি ছেলের মতো দেখতেন। তার
বাড়িতে আমি কিছুদিন পালিয়ে থাকি। কিছুদিন পর ভাবলাম, বাসায় গিয়ে
মাকে বলে ইনডিয়া চলে যাবো। মা জানতেন আমি সাইক্লোস্টাইল মেশিন তৈরি
করেছি এবং লেখা ছাপি। কিন্তু বাবা কিছুই জানতেন না।
২৩ জুলাই বাসায় আসার পর মা বললেন, আজকে রাতটা থেকে কাল চলে যাস।
পাকিস্তানিদের কাছে আমার বাড়ি ফেরার খবর চলে যায়। ওই রাতেই
ক্যাপ্টেন ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তানি আর্মি বাসা ঘিরে ফেলে।
আর্মির হাতে আটক হই। আমি খুবই তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হয়ে এলাম।
কারণ আমি যদি না যাই তাহলে ঐ সাইক্লোস্টাইল মেনিশটা এবং ছাপার কোনো
না কোনো কাগজ পেয়ে যাবে। তারা আমাকে পেয়ে বাড়ির ভেতর দেখলেও মেশিনটি
যেহেতু খোলা অবস্থায় ছিল তাই কিছু বুঝতে পারেনি।
আমাকে ওরা ট্রাকে তুললো। গাড়িতে এসে রিজওয়ান নামের একটা ছেলেকে
দেখলাম যে আমাদের সঙ্গে ঢাকা কলেজে পড়তো। পরবর্তীতে ওকে আমি আর
দেখতে পাইনি। ধানমন্ডি থেকে আরও একটি ছেলেকে নিল।
ওরা প্রথমে নিয়ে গেল ছোট্ট একটা ঘরে। ছোট বাথরুমের মতো আকার। ওখানে
১৫-২০ জন লোক ছিল। বসার কোনো অবস্থা ছিল না কারণ বসতে গেলে জায়গা
হবে না। বন্দিজীবনে কয়েকটি জায়গায় তারা আমাকে নিয়ে যায়। চোখ বেঁধে
নিতো। তাই কোথায় যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারতাম না।
প্রথম নির্যাতন করার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পরে বেধে ওরা শাস্তি
দিত। ওরা আমার পাঞ্জাবি খুলে নেয়, চুল ন্যাড়া করে দেয়। আমাদের
চাবুক দিয়ে পেটাত। এক জায়গায় আর্মিরা দরজা দিয়ে ঢুকেই আমাদের মারা
শুরু করতো। ওই রুমের পেছন দিয়ে কিছু ঘর ছিল। সেখান থেকে নির্যাতনের
শব্দ আমরা পেতাম। এখানে অত্যাচারের অনেক ধরনের জিনিস ছিল। ছাদের
উপর রড ছিল। রডের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে আমাদের পেটাতো। প্রায় সময়ই
অজ্ঞান হয়ে যেতাম। মাঝে মাঝে ছাদের পিলারের রডের সঙ্গে দড়ি দিয়ে
বেঁধে পা ওপরে মাথা নিচে করে পেটাত। ওখানে যে দেয়ালটা ছিল সেখানে
সমস্ত রক্তের দাগ লাগত। তারা কতো অত্যাচার করেছে। কখনো কখনো অফিসে
নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক শক দিত। মেঝেতে ফেলে মাথার ওপর বুট রেখে আমাকে
জিভ দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করিয়েছে। বলেছে, বাংলাদেশ বানাও।
ছোট্ট একটা বাটিতে আমাদের লবন ছাড়া ভাত দিত। যারা রান্না ঘরে কাজ
করার সুযোগ পেত তারা মাঝে মাঝে এক টুকরো পেঁয়াজ লুকিয়ে নিয়ে আসতো।
তাদের ছিল সেটা সবচেয়ে আনন্দের খাবার! অত্যাচারে হাতের সমস্ত চামড়া
উঠে গিয়েছিল। ভাত খেতে গেলে ভীষণ জ্বালা করত। আর সেই বাটিতেই আমরা
পশ্রাব করতাম, পায়খানা করতাম।
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আমাদের ওপর যে অত্যাচার করা হতো তা দ্বিতীয়
মহাযুদ্ধের যে সব ছবি আমরা দেখি তাকে হার মানিয়ে যাবে। প্রতিদিন
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের মারত। আমার এখনো মনে আছে, অজ্ঞান
হওয়ার পরেও আমাকে ছাদের রডের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল।
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় আমাদের যে শেডে রাখতো তার বাইরে একটা
পানির কল দিয়ে অল্প অল্প পানি পড়ত। ওটার নিচে সারি বেঁধে আমাদের
নিয়ে যেতো। যখন পানির ট্যাপের নিচে যেতাম সঙ্গে সঙ্গে পেটানো আরম্ভ
হতো। যেন বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে না পারি। এটাতেই ওরা গোসল বলত।
দশ বছরের একটা ছেলের কথা মনে পড়ে যাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়।
অকথ্য নির্যাতনে তার ব্রেইন ড্যামেজ হয়ে যায়। ছেলেটি ছিল বোবা।
আমাকে যখন প্রথম নিয়ে যায় তখন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে আমাদের
মারত। আমাকে যতটুকু মারতো তার চেয়ে ওকে বেশি মারত। ওকে যখন মারত,
তখন ও কোন কথা বলতে পারতো না। আমাকে মারার সময় কোনো প্রশ্ন করলে
বোঝাতাম যে আমি কথা বলতে পারি। যেহেতু কথা বলছে না তাই মার খেতে
খেতে আমার সামনে একদিন ওর নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মারা গেল চোখের
সামনে।
সারাদিন নির্যাতনের ফলে রাতের বেলায় একজন শুধু শব্দ করেছিলেন,
আল্লাহ বলে । এ শব্দ শুনে রাতে আর্মিরা তাকে ধরে নিয়ে যায় চিৎকার
করার অজুহাতে। তাকে নিয়ে গিয়ে মেরেছিল, তার মারের শব্দ আমরা
শুনেছি। তারপর তাকে যখন আমাদের কাছে ফেলে দিয়ে যায় তখনও তার শরীর
দিয়ে রক্ত ঝড়ছিল। তিনি আমার কোলেই মারা যান।
এখানে অত্যাচারের ধরণটা ছিল ঘরের মধ্যে আটকে রেখে কেউ লাঠি দিয়ে বা
কেউ বেল্ট দিয়ে আমাদের মারত। একটা প্লেটে করে আমাদের খাবার দিত।
এখান থেকে যখন কাউকে নিয়ে যেত কেউ কেউ ফিরে আসত, কেউ কেউ ফিরে আসত
না। আমরা প্লেট গোনার পর বুঝতে পারতাম কতোজন আমাদের মাঝ থেকে
হারিয়ে গেলেন!
আমরা যে টিনের শেডে থাকতাম সেটাতে বাঁশের ক্ষেরা করা ছিল। আমি
থাকতাম মাঝেরটায়। বাকি দুই পাশে আরো দুটো রোম ছিল অর্থাৎ মোট
তিনটি। আমাদের সকাল বেলা কাজ করতে নিয়ে যেত। একে বলতো ওরা
ফিল্ডওয়ার্ক। মিলিটারি কোয়ার্টারের আশে পাশে অনেক জঙ্গল ছিল।
কাটাগাছে ভর্তি ছিল এলাকাটা। ওগুলো আমাদের খালি হাতে পরিষ্কার করতে
হতো। এর ফাঁকেও লুকিয়ে সিগারেট খেতেন কেউ কেউ। যারা সিগেরেট খেতেন
তাদের খুব আনন্দ দেখতাম। লাইন করে সবাই দাঁড়াতেন আর একটা টান মেরে
একেক জন চলে যেতেন।
একবার আমাকে এক আর্মি অফিসারের বাড়ি পরিষ্কার করতে নেয়। কুকুরের
মতো আচরণ করছিল তারা আমার সঙ্গে। বাইরের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করার পর
আমি বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার করছিলাম। এমন সময় সেই বাড়ির অফিসারের
স্ত্রী হঠাৎ সেই রুমে ঢোকেন। সরাসরি তার চোখে আমার চোখ পড়ে যায়।
তিনি স্থির হয়ে যান। তার চোখে অবিশ্বাস এবং ভীতি দুটোই দেখা যায়।
তার চোখের সে চাহনি আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না।
বিপরীত কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছে আমার। একবার আমার জ্ঞান ফেরার পর দেখি
ওখানকার যে সুবেদার মেজর বা প্রধান তিনি তার পায়ে আমার মাথাটা রেখে
হাত বোলাচ্ছেন। তার মুখটা ছিল অনেকটা কুকড়ানো মাংশাসী বুলডগের মতো।
তার চেহারা ছিল ভাবলেশহীন। আমি বেশ অবাক হলাম, তিনিই তো আমাদের
মারেন। তাহলে এখন আবার হাত বোলাচ্ছেন কেন?
আসলে আমার মনে হয় তারাও আমাদের ফিল করতে পারতেন। অন্যায় কিছু যে
তারা করছেন এটা হয়তো অনুভব করতে পারতেন। এটা না দেখলে বোঝা যাবে না
যে মানুষ যত খারাপই হোক না কেন, তার ভেতরের মনুষ্যত্ববোধ কিছুটা
হলেও বেঁচে থাকে। হয়তো ঐ লোকটাও মনে মনে চাচ্ছিল যে অন্যায় কিছু
করা না হোক। তিনি ইংরেজি বলতে পারতেন না। তিনি ছিলেন খাস পাঠান।
তার ভাবভঙ্গিতে বুঝতাম তিনি আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসেন।
আমাদের যখন এমপি হোস্টেলে নিয়ে যায়, ওখানে অত্যাচার করে ফিরিয়ে দেয়
তখন কিয়ানি নামে এক পাকিস্তানি সেনা অফিসার আমার ঘরে এসে বলতো,
কেমন আছ।
আমি ঠিক বুঝতাম না। এটা কী সত্যিই অনুভব করতো নাকি চালাকি ছিল।
একজন লোকের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যে সে আসলে বন্দী নয়। আমার
সঙ্গেই তাকে রাখা হয়। আমি মাটিতে শুয়ে থাকতাম। সে প্রায় সময়ই বলতো,
দেখো আমাকে ধরে নিয়ে আসছে। আমি এটা করি নাই।
অর্থাৎ সব সময় সে নিজের কথাই বলতো এবং আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতো
তুমি কি করেছো, কেন করেছো ইত্যাদি।
আমার কাছে মনে হচ্ছিল সে একজন পাকিস্তানি গুপ্তচর। ভেতরে ঢুকে তথ্য
যোগাড় করছে। সে দুই-তিনদিন ছিল ওখানে। তৃতীয় দিন যাওয়ার পর আর ফিরে
আসে নি। যাওয়ার আগে আমি তার হাত ধরে বললাম, দেখুন, আপনি বলতে পারেন
আমার কেসটা কোথায়।
সে বললো, আমিও তোমার মতো বন্দী। আমি কি জানি?
আমি বললাম, আপনি যাই করেন, আমাকে খুন করবেন না।
তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোমাকে একটা কথা বলে দিতে পারি।
ওরা তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানে না।
আমি বললাম, তার মানে কি?
সে বলল, ওরা তোমার সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না।
তোমার ওপর আরও নির্যাতন হবে, যদি তুমি কিছু জানো বলে দিও। আর যতণ
পর্যন্ত তুমি কিছু না বলবে ওরা তোমাকে নির্যাতন করতেই থাকবে। কারণ
ওরা তোমার কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। হয়তো তোমাকে মেরেও ফেলতে
পারে।
আমাকে তার পরের দিন ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়। ইলেকট্রিক শকের জন্য
আলাদা ঘরে নিয়ে যেত, চেয়ারে বসিয়ে শক দিত। হাত পা বেঁধে শকের আগে
এবং পরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো যাতে আমার বক্তব্য বদলে যায়। আমার
কথা বদল হয়নি। তারপরের দিন সাদা মিলিটারির পোশাক পরা একজন অফিসার
এসে আমাকে বললেন যে, এটাই তোমার লাস্ট চান্স। তোমাকে বলতে হবে যে
তুমি কি করেছ?
উত্তর না পেয়ে আমাকে মারা আরম্ভ করলেন। আমি পড়ে গেলাম নিচে। তারপর
দাঁড়াতে বলে আবার মার। আমাকে আবার দাঁড়াতে বললেন। আমি নিজেই
দাঁড়ালাম। আবার মার। হঠাৎ তার চোখের দিকে তাকালাম। তিনি কী মনে করে
মার বন্ধ করে দিলেন।
ওদের কাছে তথ্য ছিল আমি কিছু করেছি। কীভাবে করেছি, কোথায় করেছি এর
কোনো খোঁজ বা অকাট্য প্রমাণ তারা পায়নি। আমি তখন নিজেকে এমনভাবে
কন্ট্রোল করেছিলাম যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে। সীমাহীন
নির্যাতনের মধ্যেও আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের করতে পারেনি। এই
শিক্ষাটা পরবর্তী জীবনে খুব কাজে এসেছে।
আমাকে একদিনের জন্য নিয়ে যায় সেকেন্ড ক্যাপিটাল অর্থাৎ সংসদ ভবনের
ওখানে, এমপি হোস্টেল। এমপি হোস্টেলে নিয়ে আমাকে বলা হলো, তুমি বসে
লিখো তুমি কি করেছিলে।
লেখার পরে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা খুব নির্জন ছিল। বাইরের কোনো
শব্দ ঢুকত না। তারা আবার আমাকে নির্যাতন শুরু করলো যা পেরেছে তা
দিয়েই।
ক্যান্টনমেন্টে বন্দি শিবিরে আমাদের আরেকটি কাজ ছিল। সেটা হলো কবর
খোঁড়া। সেখানে অনেক লাশ ফেলতো তারা। একবার কবর খুঁড়তে হলো আমাদের
নিজেদের জন্য। দিনটি ছিল ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
কবর খুঁড়িয়ে সেখানে আমাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। যখন
ব্রাশফায়ার শুরু করবে এমন সময় প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি শুরু হলো।
সারাটা আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। এর মাঝেই তারা ব্রাশফায়ার শুরু করলো।
আমি কেমন করে যেন আগেই কবরে পড়ে যাই।
এটা ছিল সন্ধ্যার সময়। অন্ধকারে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলে
মিলিটারিরা ভেতরে চলে যায়। তারা কবরে উঁিক দিয়ে আর পরীক্ষা করেনি
কেউ বেঁচে গিয়েছে কিনা। যেহেতু জায়গাটা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর তাই
কেউ পালাতে পারবে না এটা ওদের বিশ্বাস ছিল।
অন্ধকার আরো বেড়ে যাওয়ার পর ঝুঁকি নিয়ে আমি কবর থেকে বের হলাম।
বিষয়টি মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি। আজও মনে হয় যে, আল্লাহর রহমতেই
আমি বেঁচে এসেছি। নিজের শক্তি কিছু ছিল না। ভয় বা অন্য কিছুতে আমার
কোনো অনুভূতি কাজ করছিল না। মাথায় তখন একটিই চিন্তা, আমাকে পালাতে
হবে।
আমি নিজেকে সামলে গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে আসলাম। রাত পর্যন্ত পালিয়ে
থাকলাম গাছের পাশে। এভাবে ধীরে ধীরে ক্যান্টনমেন্টের মেইন গেট
পর্যন্ত আসলাম। যেটা এখন জাহাঙ্গীর গেট নামে পরিচিত। সেখানে খুবই
ভয় পেলাম, কারণ আর্মিরা প্রতিটি গাড়ি সার্চ করছে। আমার মাথায় চুল
নেই, গায়ে কাপড় নেই, শুধু একটা নেংটির মতো কাপড় রয়েছে। দেখলেই বোঝা
যায় আমি কোনো এক জায়গায় বন্দি ছিলাম। কি করে আমি ঐটুকু পথ পার
হয়েছিলাম তা মনে হলে মাঝে মাঝে এখনো রাতে ঘুম হয় না। দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের ছবি দেখলে যে রকম পালিয়ে আসার ভয়ের দৃশ্য দেখা যায়।
সেই মুহূর্তে ঐটুকু পথ পাড়ি দেয়া ছিল আমার জীবনের অন্যতম কঠিন
যাত্রা। দেয়ালে ছোট্ট একটা কাটা জায়গা ছিল যা দিয়ে লেবাররা যাওয়া
আসা করত। মূল প্রবেশ দ্বারটা একটু বাঁকা ছিল। আমি মাঝামাঝি গতিতে
চলতে চলতে কাটা জায়গাটা পার হতেই দেখি সেখান দিয়ে সবুজ রঙের একটা
স্কুটার যাচ্ছে। যখন মোড় নিচ্ছিল তখন সেটা খুব স্লো হলো। আমি ঝাঁপ
দিয়ে স্কুটারের মধ্যে পড়ে গেলাম। মিলিটারিরা তখন গাড়ি সার্চ করার
ব্যস্ত ছিল বলে দেখতে পায়নি। স্কুটার চালক খুব দ্রুত চালিয়ে নিয়ে
গেলেন এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি পালাচ্ছি।
আমি স্কুটার চালককে শুধু বলেছিলাম, জোরে চালান। আমাকে কিছু
জিজ্ঞাসা করবেন না।
তিনি একটি শব্দও করেননি এবং একবারও পেছনে ফিরে তাকাননি। আমি তাকে
শুধু বলেছিলাম, আসাদ গেটের দিকে যান।
বর্তমান সংসদ ভবন পর্যন্ত আসার পর সিদ্ধান্ত নিলাম এই স্কুটার নিয়ে
নিউ কলোনিতে আমার বাসা পর্যন্ত যাওয়া ঠিক হবে না। মিলিটারিরা
নিশ্চয়ই আমাকে আবার খুঁজবে। ঠিক সেকেন্ড ক্যাপিটালের সামনে আমি
তাকে থামাতে বলি। নেমে তাকে বললাম, দেখুন আমি আপনার নাম জিজ্ঞাসা
করব না। আপনিও আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনাকে ভাড়া দেয়া
আমার পক্ষে এখন অসম্ভব।
তিনি আমার কাছে পয়সাও চাননি। আমার নামও জিজ্ঞাসা করেননি। আমি আজো
জানি না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। তার চেহারাও এখন আমার মনে নেই। তিনি
আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।
তাকে বিদায় করে হেটে এলাম নিউ কলোনি পর্যন্ত। কলোনীতে ঢুকতেই
পরিচিত লন্ড্রিটা ছিল। সেখানে গিয়ে বাসার খবর জিজ্ঞাসা করলাম।
জানলাম বাসাতে আমার মা-বাবা কেউ নেই। আমি ফোনে চেষ্টা করলাম।
কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির ফলে বাবা মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না।
আমার এক দূরসম্পর্কের নানা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইন্সুরেন্স
কোম্পানি কাজ করতেন। আজিমপুরে তার বাসায় গিয়ে সবাইকে পেলাম।
মিলিটারিরা যখন বুঝতে পারলো আমি পালিয়েছি, তখন আমাকে খুঁজতে এসে
নিউ কলোনির বাসায় না পেয়ে বড় চাচার বাসায় যায়। আমি কোনো আত্মীয়
স্বজনের বাসায় থাকলে তাদেরই সমস্যা হতে পারে- এই ভেবে আমি মাকে
নিয়ে ট্রেনে করে রাজশাহী চলে গেলাম। রাজশাহীতে মায়ের এক বান্ধবীর
বাসায় গিয়ে থাকলাম।
দেশ স্বাধীন হলো। সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। রাতে
বেরিয়ে এসেছিলাম। একটা মাইক এবং রিকশা যোগাড় করলাম। মাইকটা যাদের
কাছ থেকে নিয়েছিলাম তাদের কাছে চাওয়া মাত্রই চট করে দিয়ে দিল। পরে
জানতে পারলাম দোকানের মালিকের ছেলেটি যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।
তখন বাংলাদেশের পতাকায় সূর্যের ভেতর হলুদ রঙের ম্যাপ আঁকা ছিল।
হলুদ কাপড়ের ম্যাপ কেটে হাত দিয়ে সেলাই করে আমরা পতাকা
বানিয়েছিলাম। রাজশাহী শহরে প্রথম যে বিজয় মিছিলটা বের হয়েছিল আমি
সেটাতে ছিলাম। বিজয় ঘোষণার পর আমি এবং মা ঢাকায় ফিরে আসি। এসময় আমি
খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের বাড়িটা মিলিটারিরা দখল করেছিল এবং
আমাদের বাড়িতে আমাদের নিজেদের ঢুকতেই খুব কষ্ট হচ্ছিল।
নিউ কলোনিতে ফেরার পর জানলাম মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা বিরোধীদের
খুঁজছেন। তাদের মধ্যে নিউ কলোনির চৌধুরী সাহেবও ছিলেন।
এক সময় শুনলাম ৯ নম্বর সেক্টরের মনোয়ার ভাই তার বাহিনীসহ পুরো
কলোনিকে ঘিরে ফেলেছেন চৌধুরী সাহেবকে ধরার জন্য। আমি মনোয়ার ভাইয়ের
সঙ্গে ফিরে আসার পরপরই যোগাযোগ করেছিলাম। মনোয়ার ভাই কিন্তু তখন
নিউ কলোনিতে থাকতেন না। তিনি মূলত থাকতেন রামপুরায় এবং সেখানেই
ঘাটি করেছিলেন।
নিউ কলোনিতে আমি চৌধুরী সাহেবকে বললাম, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে মারা
হবে না। কিন্তু শর্ত হলো এখান থেকে আপনাকে চলে যেতে হবে।
তিনি বেঁচে থাকতে যে কোনো শর্তে রাজি বলে আমাকে জানান।
মনোয়ার ভাই বললেন, যে লোক তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে তুমি তাকে কেন
ছেড়ে দিচ্ছ।
আমি বললাম, আমার একটা প্ল্যান আছে।
মনোয়ার ভাই যখন আমার প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাইলেন আমি তখন বললাম
যে আছে একটা প্ল্যান। আগে আপনি চৌধুরী সাহেবকে ছেড়ে দিন।
চৌধুরী সাহেবকে ছেড়ে দেয়ার কারণে মনোয়ার ভাই আমার ওপর রাগ
করেছিলেন। আমি তাকে বোঝালাম যে স্বাধীনতা পেয়েছি মানে এই নয় যে
আমরা যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলাম ঠিক সেভাবে অত্যাচার করবো।
আমি তাকে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম, আমাদের এখন একটা দায়িত্ব আছে।
তা হলো মোহাম্মদপুরের মানুষগুলোকে সেভ করা। কারণ যুদ্ধের সময় ছড়িয়ে
ছিটিয়ে থাকা বিহারিরা সবাই মোহাম্মদপুরে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা
যতটুকু সম্ভব তাদের পাহারা দিয়ে রেখেছিলাম। তা না হলে অনেক বিহারি
মারা পড়ত।
যুদ্ধের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন। এদেশটা খুব কষ্ট করে
স্বাধীন হয়েছে। যুদ্ধ হয়েছে এবং যুদ্ধ যারা করেছেন তাদের মধ্যে
যেমন বড় শিক্ষিত লোক ছিলেন তবে বেশির ভাগ ছিলেন এদেশের সাধারণ
মানুষ। শুধু মুক্তিযোদ্ধা হলেই মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্ব নিতে হবে-এটা
ঠিক না। অনেক মা-বাবা, ভাই-বোন আছেন যারা হয়তো অস্ত্র হাতে পাননি,
ট্রেনিং পাননি তারা অনেকভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের উপকার করেছেন- এটা
স্বীকার করা উচিত।
আমি নিজের কবর থেকে উঠে এসেছি। যুদ্ধের সময় মানুষের মৃত্যু আমার
কোলো হয়েছে। আমি মৃত্যুর আগে মুখে পানি তুলে দিয়েছি। তাদের চোখগুলো
জ্বলজ্বল করে আমার কাছে ভাসে। মুুক্তিযুদ্ধের পরে তাদের কথা স্মরণ
করেই মেডিকেলে পড়ার সময় কাউকে কিছু বলতাম না। কারণ এসব কথা ‘যুদ্ধ
করেছি’ বলে আত্মঅহংকার হবে। এই জিনিসটি যেন আমার মধ্যে না আসে। আমি
কী করেছি! তারা তাদের জীবন দিয়েছেন। এটা যে কতো কঠিন ও বেদনাদায়ক
অনুভূতি তা বোঝানো অসম্ভব।
[লেখক পরিচিতি
আমেরিকার নোভা সাউথইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ মায়ামিসহ বেশ
কিছু ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডা. সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ মানব সেবার ব্রত
নিয়ে চিকিৎসা পেশাকে বেছে নেন। দেশে এবং প্রবাসে তিনি তার পেশায় আন্তরিকতা
এবং সততার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।
তিনি কলেজ ছাত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দী
শিবিরে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। মুক্তিযুদ্ধে তার উদ্ভাবিত হাতে তৈরি
সাইক্লোস্টাইল মেশিনে মুক্তিযুদ্ধের অনেক জরুরি এবং গোপন তথ্য নিয়মিত
প্রকাশিত হয়। এই মেশিন পরবর্তী সময়ে তাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়।
গবেষক ও আবিষ্কারক হিসেবেও দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। একজন
মানুষের জীবন কতোটা বৈচিত্র্যময় হতে পারে তার একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে
এই বইটি। জীবনের দুঃসময়ে ভেঙে না পড়ে তা কাটিয়ে ওঠার প্রেরণা হিসাবে বইটি
কাজ করবে। জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবার অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে সীমিত কলেবরের
এই বইটির পাতায় পাতায়। ব্যক্তিজীবনে সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ একমাত্র মেয়ে
ও স্ত্রীকে নিয়ে মায়ামিতে বসবাস করেন।]
|