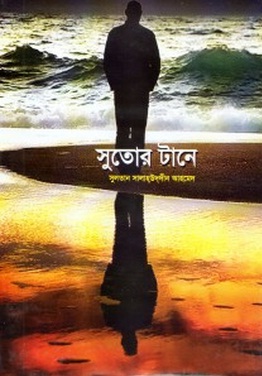|
সুতোর টানে-১
সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ
বিস্ময়ে জাগে
প্রাণ
প্রতিটি মানুষের মতো আমিও অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছি।
নতুন ভুবন আমাকে কতোটা মুগ্ধ করেছিল তা বলতে পারবো না। তবে
জীবনযাত্রার শুরুর মুহূর্তটি থেকেই আমি কয়েকজন অসাধারণ যাত্রাসঙ্গী
পেয়ে যাই। যারা কঠিন পৃথিবীর নির্মমতা ও কঠোরতা থেকে আমাকে
সচেতনভাবে আড়াল করে রাখেন।
আমার জন্ম ৭ জুন ১৯৫৩। চট্টগ্রামে। নানার বাড়ি ছিল সেখানে। নানার
বাড়ি মানে নানা সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার ছিলেন। পরবর্তী
সময়ে নানার বাড়িতে প্রায়ই আমরা স্কুল ছুটির সময়টি কাটাতে যেতাম।
ছোটবেলার স্মৃতি বলতে গেলে ঐ বাড়ির স্মৃতিটাই আমার খুব ভালো লাগে।
পাহাড়তলীতে রেলওয়ে স্টেশনের পাশে একটি পাহাড়ে ছিলো বাংলো
প্যাটার্নের বাড়ি। তার পেছনে ছিল গির্জা আর গির্জার পাশে ছিল পানির
ট্যাংক। সেখানে বিকাল বেলা যেতাম। পানির ট্যাংকে কান পেতে পানি
আসার যে শব্দ হতো তা শুনতাম। সিঁড়ি দিয়ে পানির ট্যাংকের মাথায় উঠে
যেতাম কখনো কখনো।
আমার মায়েরা ৬ বোন ৩ ভাই। অর্থাৎ আমার আটজন মামা খালা! তাদের সবার
ছেলেমেয়েসহ সবাই যখন এক সঙ্গে হতাম তখন রীতিমতো একটা হাট বসে যেত।
সারাক্ষণ হৈ চৈ করে মেতে থাকতাম আমরা।
নানা বাড়িতে ছিল বিশাল এক ডায়নিং টেবিল। নানা আমাদের সবাইকে নিয়ে
বসতেন। তিনি বসতেন টেবিলের মাথায়। আমরা সবাই পাশ দিয়ে বসতাম। এতো
বেশি আত্মীয় স্বজন ছিল যে খুব মজা হতো। সকালের নাস্তাটাও খুব মজার
ছিল। হাতে তৈরি আটার রুটি একটা করে কপালে জুটত! আর সঙ্গে চা দেয়া
হতো। আমরা চায়ের মধ্যে রুটি ভিজিয়ে খেতাম। এক রুটিতে আমাদের পেট
ভরতো না। সবাই ক্ষুধার্ত থাকতাম। তাই চিন্তা করতাম রান্না ঘর থেকে
কীভাবে আর একটা রুটি আনা যায়। আমরা তখন বিরাট এক দলের মতো ছিলাম।
আমার দলের সদস্যরা আমাকে ভালো জানতো। একারণে বোনাস হিসেবে একটা
বাড়তি রুটির অর্ধেকটাও ছিড়ে আমাকে দেয়া হতো।
তখন কেবল স্কুলে যাচ্ছি। বয়স পাঁচের মতো হবে। আমার প্রথম স্কুলের
হাতেখড়ি হয় ভেড়ামারা স্কুলে। এটা একটা প্রজেক্টের স্কুল ছিল। আমার
বাবা তখন কাজ করতেন একটা মিলে। তিনি তখন মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
অফিসার ছিলেন। বাবার কারণেই আমাদের ভেড়ামারা যেতে হয়েছিল।
চট্টগ্রামে নানার বাড়ির পাশে একটা শিমুল গাছ ছিল। সেই শিমুল গাছটার
পাশ দিয়ে ছিল পাহাড়ে নেমে আসার পথ। পাহাড়ে উঠতে আমাদের তখন কোনো
অসুবিধাই হতো না। কিন্তু খেলার জায়গা ছিল পাহাড়টা। কাজেই পাহাড়ের
পাশ দিয়ে আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে নামতাম। ওটা আমাদের একটা বিরাট ফূর্তির
বিষয় ছিল।
ওখানে রেলওয়ে হাই স্কুলে আমার মামা পড়তেন। মামা স্কুলে স্কাউটের
সদস্য হিসাবে ড্রাম বাজাতেন। আমার মনে আছে তার কাছে স্কাউটের একটি
ছুরি ছিল। সেই ছুরির মধ্যে অনেকগুলো জিনিস একসঙ্গে রাখার ব্যবস্থা
ছিল। অনেকটা সুইস আর্মি নাইফের মতো। সেটা ছিল আমার স্বপ্নের ছুরি।
মনে হতো ঐ ছুরিটা পেলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবো। অনেকটা
অ্যাডভেঞ্চার হিরোর অনুভূতি!
একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। দিনটি অবশ্য আমার মতো অনেকেরই
আতঙ্কের দিন। বিষয়টি হলো মুসলমানীর। সে কী যন্ত্রণা হাজমের হাতে!
সেদিন সকাল থেকে হঠাৎ করে সবাই আমাকে খুব খাতির করছে। আমি অবাক
হলাম কারণ যেখানে কে কোথায় আছে সেই খবর কেউ রখেছে না সেখানে আমার
এতো খাতির কেন! তারপর হাজম আসল। হাত-পা বাধাঁর পর মনে হলো, একেবারে
জল্লাদের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গ্রামে যেভাবে মুসলমানী হয়
সেভাবেই হলো।
মনে পড়ে একবার আমার খুব অসুখ হয়। অসুখে প্রচন্ড জ্বর হয়। তখন
কীভাবে জানি মামা জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর নুরুল ইসলামকে নিয়ে আসেন।
তিনি তখন চট্টগ্রামে প্র্যাকটিস করতেন। আমি জেদ ধরলাম, কোনোভাবেই
তার কাছে চিকিৎসা করাবো না। কান্নাকাটি অবস্থা। নুরুল ইসলাম সাহেব
খুব বিপদে পড়ে গেলেন কারণ আমাকে তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি ওভাবে
দেখেই ঔষধ দিয়ে গেলেন। সে ঔষধ আমাকে হরলিকসের সঙ্গে বা দুধের মধ্যে
দেয়া হতো। ঔষধ খাওয়াটা আমার জন্য তখন খুব কষ্টকর ছিল।
একবার একটা ঝড় হয়েছিল। প্রচন্ড ঝড়। ঝড়ের বেগে একটা আস্ত জাহাজ উড়ে
এসে মাটিতে পড়েছিল। সেই সময় আমরা চট্টগ্রামের বাড়িতে ছিলাম। ঝড়ে
টিনের চাল সব উড়ে গেল। বাড়ির একটু নিচে নানার পালা গরু ছিল। ঝড়ে
নানার ঐ গরুর ঘরের চালও উড়ে গিয়েছিল। আমরা তো তখন আসলে এতো কিছু
বুঝতাম না। এতোটুকু বুঝতাম যে খুব ফূর্তি হবে কারণ সারারাত ঝড় হবে।
সবাই অস্থির হয়ে আছে। বাসায় সোফা ছিল। আমরা সেটার ওপর উঠে লাফালাফি
করলাম, কেউ কিছু বললো না।
চট্টগ্রামে আমাদের কিছু ভারতীয় বাংলা বই ছিল। যেগুলো আমার খালারা
পড়তেন এবং আমাদেরও পড়ে শোনাতেন। পাগলা দাশু-র কথা মনে পড়ে যেটি
পড়তে এবং শুনতে বেশ মজা লাগতো। ট্রেজার আইল্যান্ড খুব প্রভাব
ফেলেছিল আমার মনে। এগুলো আমি খুব ছোটবেলার কথা বলছি। রবিনসন ক্রুসো
আমার খুবই ভালো লেগেছিল। কেমন করে নির্জন দ্বীপের মধ্যে একজন মানুষ
বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে। কতো সুন্দর করে সংসার গড়ে তুলেছিল সে।
শ্রীকান্ত ভালো লেগেছিল। বিশেষ করে বইয়ে রাতের বর্ণনা কখনো ভোলার
নয়।
বাসায় মুরুব্বি বলতে তখন মা, খালা, মামা, নানা-নানি ছিলেন। আমার
ডাক্তারি পাশ করার পরেও আমার নানা-নানি, দাদা-দাদি বেঁচে ছিলেন।
এটা একটা বড় পাওয়া আমার জন্য। আমরা এক ছুটিতে যেতাম নানার বাড়ি আর
এক ছুটিতে যেতাম দাদার বাড়ি।
দাদা ছিলেন খুব রাশভারী মানুষ। তার ওখানে চট্টগ্রামের মতো আনন্দ
হতো না। সেখানে অন্য ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল পরিবেশ ছিল। দাদার বাড়ি
ছিল রাজশাহী শহরেই। অলকা হলের সামনে। বাড়ির নাম ছিল প্রসন্ন ভবন।
দাদার বাড়িটা ছিল অনেকটা প্রাসাদের মতো। এখন আর ওটা নেই।
আমাকে দাদা-নানা দু’জনই খুব ভালোবাসতেন। দাদার সঙ্গে এবং নানার
সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন দাদা অন্য সবাইকে
যা বলতে পারতেন না তা আমাকে বলতেন। সাধারণত ওই সময়ের মুরুব্বিদের
সঙ্গে এভাবে কথা হতো না।
একটা কথা আমার মনে আছে। আমি একদিন মাকে গিয়ে বললাম, আমার নাম
সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ আকারে খুবই বড়ো। লিখতে অসুবিধা হয়। তাই
ছোট করে দিলে ভালো হয়।
মা আমাকে বললেন যে নামটা তার দেয়া নয় এটা দাদার দেয়া। তিনি দাদাকে
একথা বলতে বললেন। আমি দাদার কাছে গিয়ে আবদার করলাম, নামটা ছোট করে
দিতে।
দাদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, তোমার নাম কী?
আমি তখন বললাম, আমার নাম সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ। আপনি এটা
জানেন না?
দাদা তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার পুরো নাম আবু ফয়েজ সুলতান
সালাহ্উদ্দীন আহমেদ।
আমি তখন এক দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, আমার নাম ছোট করার দরকার
নেই। যা আছে তাই ভালো!
তখনকার দিনে নাম যতো বড় করা যায় ততো ভালো বলে ধরা হতো। আমার দাদা
সাতটি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজির
ডিরেক্টর ছিলেন। দাদার নাম শামসুদ্দীন আহমেদ। তার মেধা ছিল প্রচুর।
তার মেধা কতো ছিল বা তিনি কতো জানতেন তার একটা উদাহরণ দিইÑ
আমার চাচা নাজিমউদ্দিন আহমদও পরবর্তী সময়ে আর্কিওলজিতে বিখ্যাত হন।
দাদার অনেক পাবলিশড আর্টিকল ছিল। আমি এটা একদিন চাচাকে বললে চাচা
বললেন যে তোমার দাদার যে জ্ঞান তিনি এই আর্টিকলগুলো না লিখলে তা
আমাদের পক্ষে কখনো করা সম্ভব ছিল না। চাচা নিজেও দাদার লেভেলে যেতে
পারছেন না বলে আমাকে জানান।
দাদাকে দেখতাম শিলালিপি পড়তে। ইজি চেয়ারে বসে থাকতেন। ছোট্ট একটা
রেডিও ছিল সেটা শুনতেন। অনেক মানুষ আছেন যারা সব সময় পড়াশোনা বা
বই-পত্র নিয়ে পড়ে থাকেন। দাদা তেমন ছিলেন না। তিনি আমাকেও বড়
মানুষের মতো সমান গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতেন। একদিন মসজিদে মাওলানা
সাহেবরা কথাবার্তা বলছিলেন। তাদের কথা শুনে এসে আমি দাদাকে গিয়ে
বললাম, দাদা আপনি তো খুব বিদ্বান ব্যক্তি?
খুব ছোট ছিলাম, তাই দাদা খুব মজা করে হেসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ…
হ্যাঁ।
আমি তখন দাদাকে আগ্রহ নিয়ে বললাম, মসজিদে মাওলানা সাহেবরা বলছিলেন
বেহেশতে হুরপরী আছে। হুরপরী কী জিনিস?
দাদা আমাকে বললেন, তুমি বসো। আরবি ভাষায় একটা শব্দের অনেক অর্থ
আছে। আরবি ভাষার শব্দগুলো কেউ ভালো করে না বুঝে যদি সরাসরি অনুবাদ
করতে যায় তাহলে এমন জিনিস দাঁড়ায় যার কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। তাই
মাওলানা সাহেব যা বলেছেন তার ধারণা মতো তিনি এটার ব্যাখ্যা
দিয়েছেন। কিন্তু বেহেশতে কী আছে সেটা বোঝানোর মতো এমন কোনো উদাহরণ
পৃথিবীতে নেই যা দিয়ে তুলনা করা যাবে।
উত্তরটা তখন বুঝিনি। আমি ভাবলাম একটা সোজা প্রশ্ন করলাম আর তিনি
কতো কঠিন করে উত্তরটা দিলেন!
দাদাকে যখন জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে সংবর্ধনা দেয়া হয় তখন আমি সঙ্গে
ক্যামেরা নিয়েছিলাম ছবি তোলার জন্য। কিন্তু দাদা মাত্র দুই তিনটা
কথা বলেই তার বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়েন। বিষয়টা এতো দ্রুত ঘটে যে
তার ছবি তোলার সুযোগ পেলাম না। মনে পড়ে দাদা সেদিন মঞ্চে খুব ছোট
বক্তব্যে বলেছিলেন, আমি সারাজীবন যা করেছি সেটা কোনো প্রতিদান
পাওয়ার আশায় নয়।
পরে তার কাছে জানতে চাই, দাদা আপনি এতো সংক্ষেপে কেন বক্তব্য শেষ
করলেন।
তখন তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা শুধু আমার জন্য নয়, সবারই মনে
রাখার মতো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, অহংকার হচ্ছে পতনের মূল। কোনো
একটা কাজ করলে তার বিনিময়ে কোনো কিছু চেয়ো না। কাজটাই যেন তোমার
আনন্দের জন্য হয় এবং সেটাই যেন তোমার জীবন হয়। জীবনে যারা কোনো
কিছু করতে চায় তারা যেন এটাকে মেনে নেয় যে এটাই আমার জীবনের অংশ,
কিন্তু’ তার বিনিময়ে যদি প্রাপ্তির প্রত্যাশা করো তাহলে চাওয়াটা
বেড়ে যাবে।
আমার নানা এবং দাদা দুজনই দু’দিক থেকে খুব বড় ছিলেন। আমার নানা
রিটায়ার্ড করার পর চট্টগ্রাম থেকে সৈয়দপুরের গ্রামের বাড়িতে চলে
যান। সেখানে তিনি নিজ হাতে বাড়ি করেন, ক্ষেত-খামার, চাষাবাদ করতেন।
আমার কাছে খুব অবাক লাগতো যে মানুষ চট্টগ্রামের বিশাল বড় বাড়িতে
খুবই ভালো ছিলেন তিনি অবলীলায় খুব সহজ জীবন বেছে নিলেন কীভাবে। আমি
নানাকে দেখেছি নিজে মাটি মাথায় করে ফেলছেন।
আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, চল মাছ ধরবো।
উৎসাহের সঙ্গে পুকুরে মাছ ধরতে যেতেন। পুকুরে কৈ ধরে ডাঙ্গায় এনে
তিনি আমাকে ওটা ধরতে বলতেন। কিন্তু মাছ যেভাবে লাফাচ্ছে তা দেখে
আমিও ভয় পেয়ে যেতাম।
আমাকে হেসে বলতেন, তুমি হলে শহরের ছেলে। গ্রামের কিছুই জানো না।
আমি বলতাম, আপনি শহরের মানুষ কিভাবে গ্রামের মানুষ হয়ে গেলেন!
নানা তখন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন, দেখো তুমি যেখানেই থাকো,
নিজের তৈরি বাড়ি, নিজের ক্ষেতের খাবার এগুলোর মধ্যে যে আনন্দ তা
তুমি অন্য কোথাও খুঁজে পাবে না।
আলেকজান্ডার পোপ তার ১০ বছরে বয়সে একটা কবিতা লিখেছিলেন। ছেলেবেলায়
পড়েছিলাম। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে সুখী
ব্যক্তি যিনি নিজ হাতে নিজের ক্ষেতে ফসল ফলিয়ে খাবার-দাবার করেন।
নানা সহজ সরলভাবে জীবন-যাপন করতে পছন্দ করতেন।
নানা এবং দাদা দুজনেই ছিলেন খুব বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আমার
জীবনে তাদের প্রভাব খুব বেশি।
[লেখক পরিচিতি
আমেরিকার নোভা সাউথইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ মায়ামিসহ বেশ
কিছু ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডা. সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ মানব সেবার ব্রত
নিয়ে চিকিৎসা পেশাকে বেছে নেন। দেশে এবং প্রবাসে তিনি তার পেশায় আন্তরিকতা
এবং সততার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।
তিনি কলেজ ছাত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দী
শিবিরে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। মুক্তিযুদ্ধে তার উদ্ভাবিত হাতে তৈরি
সাইক্লোস্টাইল মেশিনে মুক্তিযুদ্ধের অনেক জরুরি এবং গোপন তথ্য নিয়মিত
প্রকাশিত হয়। এই মেশিন পরবর্তী সময়ে তাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়।
গবেষক ও আবিষ্কারক হিসেবেও দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। একজন
মানুষের জীবন কতোটা বৈচিত্র্যময় হতে পারে তার একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে
এই বইটি। জীবনের দুঃসময়ে ভেঙে না পড়ে তা কাটিয়ে ওঠার প্রেরণা হিসাবে বইটি
কাজ করবে। জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবার অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে সীমিত কলেবরের
এই বইটির পাতায় পাতায়। ব্যক্তিজীবনে সুলতান সালাহ্উদ্দীন আহমেদ একমাত্র মেয়ে
ও স্ত্রীকে নিয়ে মায়ামিতে বসবাস করেন।]
|